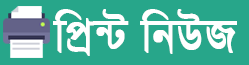দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পেছনে — সংক্ষিপ্ত ও পুনরায় বিন্যস্ত ইতিহাস

ইংরেজ আগমন ও শাসন প্রসার
ইংরেজরা প্রথম আবির্ভাব করে ১৬০১ সালে; ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ভারতে ব্যবসার ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। প্রথমে বাধশা জাহাঙ্গীর তাদের বিশ্বাস করে নানা সুবিধা ও জমি পানামধ্য দিয়ে ইংরেজদের ক্ষমতা বেড়ে ওঠে। শতবর্ষের মধ্যেই তারা দেশে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা অঞ্চল শাসন করতে থাকে — ১৭১৭, ১৭৪০ সালের মধ্যে তারা আরও বিস্তার লাভ করে। শেষপর্যায়ে ‘দেশ বাদশার, আইন আমাদের, শাসনযোগ্যতা কোম্পানির’—এমন বাস্তবতাই বিরাজ করে।
প্রতিরোধ ও আলেমদের প্রতিক্রিয়া
দিল্লির হাদিসবিদ শায়খ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি (রহ.) তার ছাত্র-শিষ্য সমাজকে সতর্ক করেন—ইংরেজ শাসন দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং এটি মুসলিম সমাজের জন্য বিপজ্জনক হবে। তার কৃতিত্ব ও সতর্কবার্তা পরবর্তীতে বহু আলেমের মধ্যে আন্দোলনের বীজ বোনা শুরু করে।
তার ছেলের কন্যা-সন্তান ও শিষ্যরা—বিশেষত শাহ আবদুল আজিজ—ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জোরালো ফতোয়া দেন। শাহ আবদুল আজিজ ১৭৭২ সালে ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষ এখন ‘দারুল হরব’—অর্থাৎ মুক্ত করতে জিহাদ ফরজ, এবং পরে তার ও তার অনুরাগীদের সক্রিয় প্রতিরোধ শুরু হয়।
টিপু সুলতানও (মহিষুর রাজ্যের বিপুল প্রতিরোধক) ইংরেজদের বিরুদ্ধে রণসংগ্রামে নামেন; তিনি ১৭৯৯ সালে শহিদ হন। এ সময়ে মুসলিম সমাজে খানিক বিভক্তি তৈরিও হয় — কিছু নেতা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় লোভে পড়ে মিত্রতা করে ফেলেন, অন্যরা抵抗 অব্যাহত রাখেন।
বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা (পলাশী—মীর জাফর)
পলাশীর যুদ্ধ হলো ইংরেজ শাসনের স্থায়ীত্বের এক মাইলফলক। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে মীর জাফরকে অর্থের বিনিময়ে কৃত্রিমভাবে নিয়োজিত করা হয়; এর ফলে স্বাধীন শক্তির পতন ঘটে এবং স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিতের পথ শুরু হয়।
পাঞ্জাব, দিল্লি ও নৃশংস নির্যাতন
১৮শ শতকের পরে পাঞ্জাব জয় করে রাজা রঞ্জিত সিং মুসলমানদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালান — মসজিদ ধ্বংস, পরিবারে জুলুম ইত্যাদি। এ ঘটনার বিরুদ্ধে উঠে আসেন সাইয়্যিদ আহমদ ব়েরেলভি; তিনি বহু মুজাহিদ নিয়ে পাঞ্জাবে লড়াই শুরু করেন এবং ১৮৩১ সালের বালাকোট যুদ্ধে শহিদ হন।
এ সময়কাল নানান আলেমদের ওপর ইংরেজদের দমন-পীড়ন ও হত্যা-নির্যাতনের কালপর্বে পরিণত হয়। ১৮৬৪–৬৭ সালের মধ্যে প্রচলিত তথ্যানুসারে হাজারো আলেমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়—এই ভূমিকা মুসলিম সমাজে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।
স্বাধীনতা আন্দোলন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন
ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক বদল আনে—ফার্সি ও ধর্মীয় শিক্ষার স্থান দখল করে ইংরেজি নাগরিক শিক্ষার জোরালো প্রবর্তন। লর্ড ম্যাকোলের মত নীতিমালা ভারতীয় শিক্ষা-চেতনায় বিলেতি মূল্যবোধ প্রবেশ করায় এবং মুসলিম সমাজকে আর্থিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এগুলোই একদিকে ছিল রাজনৈতিক শোষণ, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অবক্ষয়ের কারণ।
আলেমদের সংগঠন, ১৮৫৭ ও রেশমি রুমাল আন্দোলন
১৮৫৭ সালের উত্তেজনাপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ও পরবর্তী রেশমি রুমাল আন্দোলনে বহু আলেম ও ধর্মীয় নেতার সক্রিয়তা ছিল—মুহাজিরে মক্কি, মাওলানা কাসেম নানুতবি, মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি প্রমুখের নেতৃত্বে বহু আন্দোলন ও লড়াই সংঘটিত হয়। যদিও সেগুলো সফলভাবে স্বাধীনতা আনতে ব্যর্থ হয়, তবু আলেম সমাজের প্রতিরোধ ও ঐক্যের ইতিহাস গঠন করে।
দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট
এ দীর্ঘ, হৃদয়বিদারক ও প্রতিকূল ইতিহাস—রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক-আর্থিক অবক্ষয়, আলেমদের ওপর দমন ও শিক্ষার পরিবর্তন—ই ছিল দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল প্রেক্ষাপট। ১৮৫৭-এর পরের পরিস্থিতি, আলেম সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন এবং ইসলামী শিক্ষা ও মর্যাদা রক্ষা করার তাগিদই শেষপর্যায়ে দেওবন্দের মত প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটায়। দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা ছিল কেবল একটি শিক্ষাসংস্থার জন্ম নয়—এটি ছিল আত্মরক্ষা, পুনর্গঠন ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস।
© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০২৫